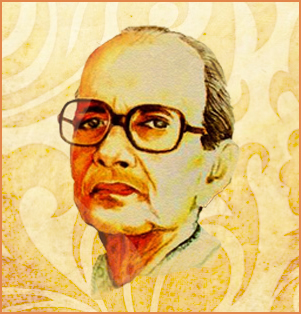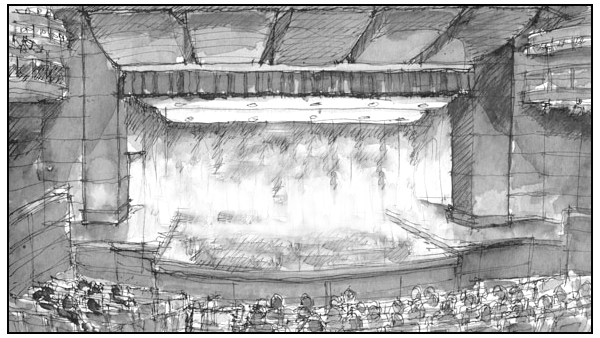ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী
একজন বিশ্ববন্দিত নাট্যকার আর একজন পৃথিবী বিখ্যাত রাজনীতিবিদ।
দুজনেরই জিহ্বাগ্রে সরস্বতী এবং দুজনেই নোবেল ল’রিয়েট। একজন তো আবার ওয়ান অ্যান্ড দ্য ওনলি ওয়ান যাঁর ঝুলিতে নোবেল আর অস্কার দু-দুটো শিরোপাই আছে।
তবে নাট্যকার ব্যক্তিটি ছিলেন রাজনীতিবিদটির চরম সমালোচক। তবে নিজের নতুন নাটকের প্রিমিয়ারে নাট্যকার টেলিগ্রাম করে নিমন্ত্রন করেছিলেন সেই রাজনীতিবিদকে।
১৯১৩ সালে বার্নাড শ’ তাঁর “পিগম্যালিয়ন” নাটকের প্রথম শো’র আগে টেলিগ্রাম করলেন চার্চিলকে :
“Reserving two tickets for you for my premier. Come and bring a friend….if you have one!”
Pat came the reply from Churchill, ”Impossible to be present for first performance. Will attend the second……if there is one!”
JU Alumni-র “মেঘপিওন” সাহিত্য পত্রিকার জন্য সুশান্তর নির্দেশে বাংলা নাটক সম্পর্কে লিখতে বসে মনে হচ্ছে কলার ভেলায় চড়ে সমুদ্রপাড়ি দিতে চলেছি। এই গুরুগম্ভীর বিষয়ের ওপর লেখার জন্য আমার মতো একজন ম্যাঙ্গো-ম্যান পটলবাবুর ওপর কেন দায়িত্ব দেওয়া হলো তার সঠিক কারন খুঁজতে গিয়ে আমার পরিবারসহ নিকট আপনজন এবং বন্ধুবান্ধব সকলেই দেখছি বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাদের ধারনা আমি যে বিষয়ে যত কম জানি সেই বিষয়ে আমি তত বেশী অগ্রগামী।
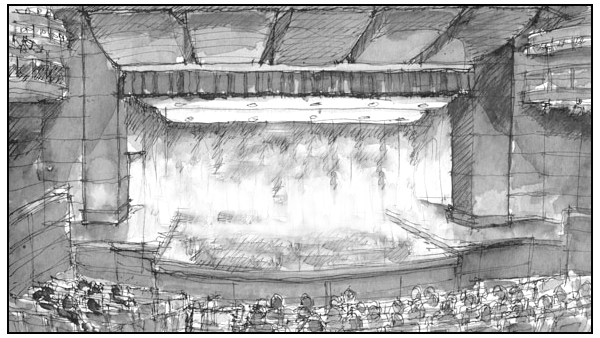
অবশ্য ওনাদের এই ধারনার যে একবারেই কোন ভিত্তি নেই একথাটা মোটেই বলা যাবে না। কারন আমার স্কুল জীবনের একটা ঐতিহাসিক নাটুকে ঘটনার কথা কি করে যেন আমার বাল্যবন্ধুরা আমার স্ত্রীর কানে তুলে দিয়েছিল। আর তারপর থেকেই ঘটনাটা এত ব্যাপক প্রচার পায় যে শুধু মাতৃভূমিতেই নয় হিমালয় পবর্ত আর সাত সাগর পেরিয়ে এই বিশ্বায়নের যুগে সবর্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে।
ঘটনাটা একটু ছোট করে এখানে বলে নেওয়া যাক।
ক্লাস সিক্সে একবার আমাদের স্কুলের বাৎসরিক উৎসবের ঐতিহাসিক নাটকে এক দূতের চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলাম। নাটক যখন জমে দই তখন একটি দৃশ্যে মহারাজ মঞ্চে উপস্থিত, সঙ্গে মন্ত্রী। রাজ্যের সীমানায় যুদ্ধ চলছে তাই মহারাজ ভীষণ উদ্বিগ্ন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সেনাপতি সেই রাত্রে সংবাদ বাহকের মাধ্যমে যুদ্ধের পরিস্থিতি বিস্তারিত জানিয়ে মহারাজকে একটি পত্র প্রেরণ করবেন। সেই সংবাদের আশায় মহারাজ আর মন্ত্রী দুজনেই উৎসুক।
এমন সময়ে দৌবারিক এসে মহারাজকে সংবাদ দেয় যে রাজসেনাপতির সংবাদ বাহক মহারাজের দর্শণ প্রার্থী। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মঞ্চে প্রবেশ।
স্টেজে ঢুকেই সামনে অত লোক দেখে আমার হঠাৎ সব কেমন যেন গুলিয়ে গেল।
ইতিমধ্যে মহারাজ বার দুয়েক প্রশ্ন করে ফেলেছেন,”যুদ্ধের কি বারতা আনিয়াছ তুমি?”
আমার মুখ থেকে কোন উত্তর নেই। হাতে একটা গোটানো কাগজ ছিল সেটা মহারাজকে দিয়ে শুধু বলতে হবে,”মহারাজ, সেনাপতি এই পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন।“ এটা বলেই দু পা পিছিয়ে এসে একবার মহারাজকে আর একবার মহামন্ত্রীকে কুর্ণিশ করে চলে যাবার কথা।
কিন্তু তখন সব গুলিয়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে। পেটের মধ্যে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। সবাই আমার দিকে উৎকন্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারছি উইংসের পাশ থেকে আমাদের নাটকের পরিচালক ইতিহাস স্যর আমাকে কিছু বলার চেষ্টা করছেন কিন্তু আমার কানে তখন কিছুই ঢুকছে না।
একসময়ে হঠাৎ যেন নিজের ভিতর থেকে একটা তাড়না অনুভব করলাম। তারপর বলতে শুরু করলাম,”যুদ্ধের বারতা আমি আপনাকে শোনাই মহারাজ। যুদ্ধক্ষেত্রে সে কি ভয়ানক যুদ্ধ চলছে। সে এক ভয়াভহ যুদ্ধ! মানুষে-মানুষে যুদ্ধ, হাতিতে-হাতিতে যুদ্ধ, ঘোড়ায়-ঘোড়ায় যুদ্ধ, তলোয়ারে-তলোয়ারে যুদ্ধের টং-টং আওয়াজ সারা যুদ্ধক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে। হাতি আর ঘোড়ার পায়ের ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। তারপর…।“
তারপর ইতিহাস স্যর আমাকে আর এগোতে দেন নি।
আলো নিভিয়ে দিয়ে আমার ঘেঁটি ধরে এক ঝটকায় উইংসের ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন।
এরপরের ইতিহাস এতই উত্তেজনাপূর্ণ ছিল যে আমি আর তা মনে করতে চাই না। এই হলো আমার জীবনে বাঙলা নাটকের প্রথম আবির্ভাব।
(২)
তা এইরকম এক অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন আমাকে বাংলা নাটকের ওপর লেখার অনুরোধ সামলাতে হয় তখন কি পরিমাণ দুঃসাহসিকতার পরিচয় আমাকে দিতে হবে সেটা নিশ্চয় সুধী পাঠকবৃন্দের অনুমান করে নিতে অসুবিধা হবার কথা নয়।
যাইহোক লিখতে যখন হবেই তখন বাংলা নাটকের আদিপর্বের ইতিহাসের কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে দেখা যাক। সেই কবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়েছি তার ওপরে তো শুধু ভরসা করলে চলবে না, হাতের কাছে গুগুল জেঠূ যখন আছেন যখন চিন্তা কি!
তবে বছর দুয়েক আগে কলকাতার বহুরূপী নাট্যদলের আয়োজিত নাট্যমেলাতে “মুখোশের মুখ” নাটকটি দেখতে গিয়ে সেই নাট্যউৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত একটি নাটকবিষয়ক স্মারক পত্রিকা আমার হাতে আসে। সেটাতে দেখছি শম্ভু মিত্র মহাশয়ের একটি দামী লেখা আছে এবং তাতে বাংলা নাটকের ইতিহাসের ওপর বেশ কয়েকটা কথা আছে। সেগুলোই প্রথমে পাঠকদের সাথে, ঐ কি যেন বলে, হ্যাঁ শেয়ার করে নেওয়া যাক।
১৭৭৪ সালে কলকাতা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী হবার ঠিক একুশ বছর পর ১৭৯৫ সালের নভেম্বর মাসে গেরাসিম লেবেডফ নামে এক রাশিয়ান ভদ্রলোক কলকাতায় এক মঞ্চ নির্মান করেন। এরপর সেই ভদ্রলোক একটি বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাটকটির নাম ছিল “কাল্পনিক সংবদল” – এটি একটি “দি ডিসগাইজ” নামক এক ইংরেজি নাটকের বাংলা তর্জমা।
সবচেয়ে বড় কথাটা হচ্ছে লেবেডফের এই নাটকে স্ত্রী চরিত্রে মেয়েরাই অভিনয় করেছিলেন এবং টিকিটের মূল্য ছিল চার টাকা আর আট টাকা।
প্রথমবারের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে লেবেডফ পরের বছরের মার্চ মাসে আবার এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটক অভিনয়ের আগে লেবেডফ ক্যালকাটা গেজেট কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেন; বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ ছিলঃ
“দর্শকদের সুবিধার জন্য বসিবার আসন দুইশত করা হইয়াছে যাহা শীঘ্র পুর্ণ হইয়া যাইবে। দর্শণপ্রার্থীদের এক স্বর্ণমোহর সহযোগে আবেদন করিতে হইবে। পেক্ষাগৃহ পুর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আবেদন পত্র গৃহীত হইবে।“
একটি টিকিটের জন্য এক স্বর্ণমোহর এই সময়েও আমাদের সবাইকে চমকে দেবে! তবে লেবেডফ সাহেব অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। অভিনয়ের পরের দিন তিনি আবার ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়ে দর্শকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য অকুন্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
এরপর লেবেডফ সাহেব ইংল্যান্ডে চলে গেলে বাংলা থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।
তারপর আবার উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে নতুন করে বাংলা থিয়েটারের কথা শোনা যায় – হিন্দু থিয়েটার স্থাপন এবং নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ তৈরী হয়।
এই সময়কার থিয়েটার বলতে বিশেষজ্ঞরা অবশ্য যবনিকাপট সমেত প্রসিনিয়াম মঞ্চের কথাই ধরেছেন।
শম্ভু মিত্র অবশ্য তাঁর এই লেখাটাতেই বলেছেন যে পরর্বর্তী কালে অনেক নাট্য বিশেষজ্ঞ লেবেডফের এই বাংলা নাটকের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে সেটা আমাদের মতো ম্যাঙ্গো-ম্যানদের কাছে বড় কথা নয়। একজন বিদেশী বাংলা আর বাঙালির সাথে কতখানি একাত্মতা অনুভব করলে তবে এমন একটা বিশাল ঐতিহাসিক কর্মকান্ডের সৃষ্টি করতে পারেন তা ভাবতে গেলেই শিহরিত হতে হয়।
এরপর থেকেই কিন্তু বাংলা নাটক তার স্থিতিজাঢ্যতা ত্যাগ করে জঙ্গম অবস্থা প্রাপ্ত হয়।
বাংলা নাট্য জগতে যে নাটকটি সর্বপ্রথম মৌলিক নাটক হিসবে মান্যতা পেয়েছে সেটা হচ্ছে পণ্ডিত রামরত্ন তর্করত্ন রচিত “কুলীনকুল সর্বস্ব।” ১৮৫৪ সালে লিখিত এবং অভিনীত প্রথম সামাজিক নাটক।
তারপর ১৮৫৯ সালে বাংলা নাট্যমঞ্চে মধ্যাহ্ন সুর্য্যের মতো মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত আর বিশেষ কোনো নাম বা নাট্য প্রযোজনা নজরে কাড়ে না বললেই চলে। ১৮৫৮ সালে তৎকালীন কলকাতার উত্তরাঞ্চলে এক রাজবাড়িতে “রত্নাবলী” নাটকের অভিনয় দেখে মাইকেল তাঁর পরিচিত মহলে অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলেন,”রাজারা এই তুচ্ছ নাটকের জন্য কি বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন।“
(৩)
এরপরই মাইকেলের বন্ধুরা সবাই মাইকেলকে অনুরোধ করেন বাংলা নাটক লিখবার জন্য। এই সময়ে মাইকেলের সেই বিখ্যাত উক্তি আমরা স্মরণ করতে পারি,
”অলীক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।“
এরপর আমরা মাইকেলের হাত থেকে পাই তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক “শর্মিষ্ঠা”। এই নাটকটি পড়ে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং আরও জ্ঞানীগুণীজন নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।
এইখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাংলায় নাটক রচনার মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমরা প্রথম বাঙালি লেখক মাইকেলকে পাই। আর শুধু তাই নয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দ মাইকেল প্রথম প্রয়োগ করেন তাঁর পদ্মাবতী নাটকে, পরীক্ষামূলক ভাবে বলা যেতে পারে।
এরপর থেকেই বাংলা নাট্য জগতের তৎকালীন মরা গাঙে বাণ এলো মনে হয়।
মাইকেলের হাত থেকে যখন একেরপর এক নাটক, প্রহসন যখন বেরচ্ছে তখন ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্র’র “নীলদর্পণ” ভীষণ ভাবে বাংলা নাট্য জগতে এবং বৃটিশ শাসক মহলে আলোড়ন তুলে দিল।
এরপরের ইতিহাস পাদ্রি লংসাহেবের নাম দিয়ে মাইকেলের নীলদর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদ তো আমাদের সবারই জানা। অনেকদিন ধরে এই নীলদর্পণ নাটকটি বৃটিশদের বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল। সেই সময়ে সারা বাংলা জুড়ে নীলদর্পণের অভিনয় চলেছে বেশ কয়েক বছর ধরে। ১৮৭২ সালে কলকাতার সাধারন রঙ্গশালার উদ্বোধন হয় নীলদর্পণ নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এর ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে বৃটিশ শাসকদল ১৮৭৬ সালে নাট্য অভিনয় বিল পাস করে থিয়েটারের কন্ঠরোধ করে।
সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত নাকি ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই আইনটি বলবত ছিল। সুখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে এই আইনটি আর চালু নেই। তবে আজকের আইনি চিত্রটি আইন বিশেষজ্ঞরা হয়ত সঠিক বলতে পারবেন।
এরপর ১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা পাবার পর থেকে আমরা বাংলা নাট্য জগতে পাই গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বোস, রাজকৃষ্ণ রায়, অমরেন্দ্র দত্তের মতো আরও অনেক প্রতিভাশালী নাট্য ব্যক্তিত্ব। গিরিশ ঘোষ সে সময়ে নাটক পাগল বাঙালিকে নাটকে মজিয়ে দিয়েছিলেন বলা যায়। এই সময়েই বোধহয় বাংলা থিয়েটার জগতে সেই বিখ্যাত বা কুখ্যাত প্রবাদ বাক্যটি তৈরি হয়েছিল,
“যাত্রা দেখে ফাতরা লোকে / থিয়েটার দেখে ভদ্রলোকে”
এই গিরিশ ঘোষের কিন্তু নাট্যমঞ্চে প্রথম প্রকাশ ১৮৬৮ সালে দুর্গা পুজোর সময়ে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার একাদশী” নাটকের মঞ্চায়নের মাধ্যমে। নাটকের প্রধান চরিত্র নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশ ঘোষ দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়ে নেন। ঐ ধরনের ট্র্যাজিক অভিনয় দর্শক বাংলা নাটকে আগে কখনও দেখে নি। যদিও গিরিশচন্দ্রের কোনও রকম প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না কিন্তু তিনি নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ ক’রে দেশী-বিদেশী সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর থেকে গিরিশ ঘোষকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। সেই সময়ে গিরিশ ঘোষকে বাঙলা মঞ্চের জনক বলা হত। তবে একটা শুন্যতা সেইকালে বাংলা নাট্য জগতে দেখা গিয়েছিল যার কারনে নাট্যমোদি মহলে একটি কথা প্রচলিত ছিল যে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের জনক আছে ঠিকই, কিন্তু কোনো কাকা বা জ্যাঠা নেই। গিরিশচন্দ্র মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে’র নাট্যরূপও দিয়েছিলেন এবং এটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়। এই সময়েই বিনোদিনী দাসী নামে এক অতি অল্প বয়সী অভিনেত্রী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তী যুগে তিনি বাঙলা রঙ্গমঞ্চের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষের নাটক দেখে একাধারে নাট্যকার আর নটসম্রাট গিরিশ ঘোষকে আর্শীবাদ করেছিলেন লোকশিক্ষার কান্ডারি হিসেবে আর চৈতন্যলীলায় বিনোদিনীর অভিনয় দেখে তাঁকে “চৈতন্য হও” বলে আশীর্বাদ করেছিলেন।
(৪)
গিরিশ ঘোষকে আমরা মূলত জানি পৌরাণিক আর সামাজিক কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনাকার হিসেবে। তবে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে লেখেন সিরাজদোউল্লা, মির কাশেম আর ছত্রপতি শিবাজীর মতো দেশাত্মমূলক নাটক। এছাড়া উনি নিজে শেক্সপিয়ার অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করেছিলেন কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্য পান নি। আমার মনে হয় সাধারন বাঙালি দর্শক বোধহয় তখনও শেক্সপিয়ারকে হজম করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি কেননা পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি বাঙলার দর্শক ভীষণ ভাবে শেক্সপিয়ার প্রেমী হয়ে উঠেছিল যা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তবে গিরিশ ঘোষের বেশ কিছু নাটক আজও বাঙালী দর্শককে প্রভূত আনন্দ দিয়ে চলেছে।
বহুবর্ণে রঙিন ছিল গিরিশ ঘোষের বর্ণময় জীবন। এক সময় উনি লিখেছিলেন,
“তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কন্ঠের হার
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পন
হৃদে সাধ রাশি রাশি, রঙ্গভূমি ভালোবাসি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন”।
গিরিশ ঘোষের শেষ জীবনের কিছু নাটক দেখেছিলেন আর এক মহান নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ি। তখন তাঁর বয়স বড়জোর বাইশ। সেই মুগ্ধ অভিজ্ঞতার কথা তিনি তাঁর বাহান্ন বছর বয়সে শুনিয়ে ছিলেন আর এক তরুণ শম্ভু মিত্রকে যিনি পরর্বর্তী কালে এক মহান নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।
আমার মনেহয় এটাই বোধহয় বাংলা নাটকের মহান লিগ্যাসি। এক মহান নাট্যব্যক্তিত্বের প্রতিভার ছটা আর এক মহান নাট্যব্যক্তিত্ব বর্ণণা করছেন ভাবিকালের আর এক মহান নাট্যব্যক্তিত্বের কাছে যিনি তখন সবে বিকশিত হতে শুরু করেছেন।
১৯১২ সালে গিরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। গিরিশচন্দ্রের পর বাঙলা রঙ্গমঞ্চের উল্লেখযোগ্য নতুন পর্বের সুচনা হল শিশিরকুমার ভাদুড়ির আর্বিভাবে। শিশিরবাবু কলেজ জীবনে বেশ নামকরা অভিনেতা ছিলেন এবং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তাঁর নাট্যপ্রযোজনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পরে তিনি কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে পুরোপুরি নাটক জগতেই আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যোগেশ চৌধুরীর সীতা নাটক নিয়ে নিজস্ব নাট্যসম্প্রদায় গড়ে তুললেন। এইভাবে ‘নাট্যমন্দির’-এর সূচনা হলো এবং সেটি শ্রেষ্ঠ থিয়েটার রূপে গৃহীত হলো। তারপর থেকে শিশিরকুমারকে যুগান্তকারী শিল্পপ্রতিভা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমান কালের বহু নাট্য সমালোচক আক্ষরিক অর্থে শিশির ভাদুড়িকেই বাংলা নাটকের প্রথম নির্দেশক হিসেবে মান্যতা দেন। নাট্য-অভিনয়কে একটি সামগ্রিক শিল্পকর্ম হিসেবে তিনিই প্রথম বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেন। নাট্যমন্দিরে তাঁর প্রযোজনাতে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয়। তাঁর মঞ্চসজ্জা, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, আগের কালের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই বাংলা নাট্য জগতে তাঁর স্থান “নাট্যাচার্য” শিশিরকুমার হিসেবে চিরকাল অমলিন থাকবে।
অনুষ্টুপ প্রকাশনা সংস্থা থেকে অনিল মুখোপাধ্যায় রচিত “বাংলা থিয়েটার ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার” বইটির রিভিউতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,”শিশিরকুমার ভাদুড়ির অভিনয় দেখতে শুরু করি আমি ১৯৫১ সাল থেকে। সেই অভিনয় দেখার অভিঘাত আমায় এতই আন্দোলিত করে যে তার দু-তিন বছরের মধ্যেই আমি মনস্থির করে ফেলি যে আমি একজন পেশাদার অভিনেতা হয়েই জীবনযাপন করব।“
যোগেশ চৌধুরীর “সীতা” নাটকটি নিয়ে তিনি আমেরিকা পাড়ি দিয়ে তিনি বাংলা নাটকের জগতের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেন। আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে উপলব্ধ “সীতা” নাটকটির পোষ্ট আমেরিকা সফর সংস্করণের ভূমিকায় দেখছি যোগেশ চৌধুরী লিখেছেন যে প্রথমে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া না গেলেও আমেরিকায় পরর্বর্তী শো গুলোতে সীতা নাটকটি সাফল্যের মুখ দেখে। আবার শিশির ভাদুড়ির বায়োপিক লেখক সুনীল গাঙ্গুলির লেখা “নিসঙ্গ সম্রাট”-এ দেখছি আমেরিকায় “সীতা” অসফল হওয়ায় শিশির ভাদুড়ি আর্থিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। হায়দ্রাবাদে সুনীল গাঙ্গুলি এসেছিলেন JU Alumni-র ডাকে। ইচ্ছে ছিল “সীতা”র আমেরিকা সফরের ব্যবসায়িক সাফল্য-অসাফল্যর দিকটার ঐতিহাসিক সত্যটা যাচাই করে নেবার। দুর্ভাগ্যবশত উঞ্ছবৃত্তির চাপে হায়দ্রাবাদে সে সময়ে না থাকতে পারায় আমার আর এই তথ্যটা যাচাই করা হলো না।
নিজের জীবন সম্পর্কে বলেছেন শিশির ভাদুড়ি বলেছেন,”থিয়েটারের শিশির ভাদুড়ির জীবনটা – বাংলা থিয়েটার নিয়ে আমার স্বপ্ন, আমার দোষগুণ, এমনকী থিয়েটার চালানোর জন্য হুন্ডি কেটে টাকা ধার করা – সব জানতেন মহর্ষি। আমার জীবনটা খোলা পাতার মতো ছিল তাঁর কাছে। একমাত্র তিনিই পারতেন (আমার জীবনী) লিখতে।“
(অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে তিনি স্নেহবশত “মহর্ষি” বলে ডাকতেন। সীতা নাটকে তিনি মহর্ষি বাল্মীকির পার্ট করেছিলেন।)
(৫)
অনেকরকম বিরুদ্ধতার সঙ্গেই শিশির ভাদুড়িকে লড়াই করতে হয়েছে। ১৯৩৩ সালে ২৫শে জুলাই শিশির ভাদুড়ি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন পাওনাদারদের টাকা না-দিতে পারার অপরাধে এবং অবশেষে তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হন। ১৯৫৬ সালের ২৪ শে জানুয়ারি শ্রীরঙ্গমে অভিনয় করে শিশির ভাদুড়ি শেষবারের মতো মঞ্চহারা হন। এরপর বছর তিনেক তিনি কয়েকটি আমন্ত্রিত অভিনয় করতেন যাকে তিনি নিজেই নিজেকে ভাড়াটে কেষ্ট বলতেন। ১৯৫৯ সালের ৩০ শে জুন তাঁর মৃত্যু হয়……মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, “I want to die. I had enough of life.”
প্রাক-শিশির যুগে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। এরই মধ্যে ঠাকুরবাড়ির ঘেরাটোপে, পরিচিত মহলে আমন্ত্রিত দর্শকমণ্ডলীর সামনে, ঠাকুর বাড়ির সদস্য-সদস্যারা নিয়মিত ভাবে তাঁদের নাটক অভিনয় করে চলেছেন।
এই সময়ে ১৮৭৩ সালে মাত্র বারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যোতিদাদার “সৌদামিনী” নাটকের জন্য গান লিখে দিয়েছেন। প্রথমে কথা ছিল যে “সৌদামিনী” নাটকের প্রারম্ভে জ্যোতিদাদার একটা পাঠ থাকবে। মহলার সময়ে তিনি সেটা সবাইকে শোনাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে ছিলেন এবং মহলা কক্ষে এসে জ্যোতিদাদাকে বলেন যে এই পাঠটার বদলে যদি একটা গান দিয়ে নাটকটি শুরু করা যায়, তবে নাটকটা আরও বেশী আকর্ষণীয় হবে। প্রথমে জ্যোতিদাদা নিমরাজি ছিলেন কেননা নতুন করে গান লিখে সুর দিয়ে নাটকটিতে সংযোজন করে মঞ্চায়ন করা বেশ সময় সাপেক্ষ। আর তাছাড়া সাত-তাড়াতাড়ি এখন কে-ই বা গান লিখবে!
সেই শুনে কিশোর রবি পাশের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষনের মধ্যেই এই গানটি “সৌদামিনী” নাটকটির জন্য লিখে আনেনঃ
“জ্বল জ্বল চিতা, দ্বিগুন দ্বিগুন
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনই প্রানের জ্বালা।।“
আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে সেইসময়ে প্রচলিত নাটকের সমস্তরকম ফর্ম ভেঙে রবীন্দ্রনাথ যে শুধু মঞ্চে নাট্য প্রয়োগের গতানুগতিক চিন্তাধারাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছিলেন তাই নয়, বাংলা নাট্য জগতে এমন একটা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিলেন যা চিরকালীন।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর “ডাকঘর” নাটকটি লেখেন ১৯১২ সালে আর “রক্তকরবী” লেখেন ১৯২৬সালে শিলং-এ থাকাকালীন। এই দুটি নাটকই সময়ের বেড়া ভেঙে মানুষের কাছে চিরকালীন আবেদন রেখে গেছে। তাই আজ প্রায় ন’দশক পরেও রবীন্দ্রনাথের “রক্তকরবী” ফুলটি আজকের দর্শকের কাছে একই রকম তাজা।
আমরা আজও রক্তকরবীকে নিয়ে মঞ্চে যে নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা দেখতে পাই সেটা আধুনিক দর্শকদের কাছেও সমান আকর্ষনীও। মফস্বল থেকে শুরু করে কলকাতা শহরের যে কোন ছোটবড় নাট্যদলের কাছে রক্তকরবী’র আবেদন অলঙ্ঘনীয়। আমার মনে হয় সব ধরনের নাট্যদলেরই মনের গোপন কোনায় একবার অন্তত রক্তকরবী মঞ্চস্থ করবার ইচ্ছেটা সদাই জাগ্রত থাকে……একদিন না হয় একদিন……।
তাই এই হায়দ্রাবাদে বসেই এখানকার রবীন্দ্রভারতীতেই আমরা পশ্চিমবঙ্গের এক অখ্যাত নাট্যদলের “রক্তকরবী” প্রযোজনা দেখতে পাই। নাটকের প্রতি কতখানি দায়বদ্ধতা থাকলে একটি অখ্যাত নাট্যদল সুদূর পশ্চিমবঙ্গের এক অখ্যাত মফস্বল শহর থেকে রক্তকরবী নাটকটি মঞ্চস্থ করার সাহস নিয়ে হায়দ্রাবাদে আসতে পারে ভাবলেই আমি আশ্চর্যান্বিত হই। আরও আশ্চর্য হই যখন দেখি তারা রবীন্দ্রনাথের ওপর কলম চালিয়ে রক্তকরবীর রাজাকে তাঁরা Expose করে মঞ্চে দর্শকের সামনে উপস্থিত করেন। পরিচালকের তরফ থেকে এ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। নাটক শেষে পরিচালককে প্রশ্ন করি যে তিনি কি কোন বাণিজ্যিক সাফল্যের কথা চিন্তা করে রাজাকে প্রকাশিত করেছিলেন নাকি তাঁর আর কোন চিন্তাভাবনা এর পেছনে কাজ করেছিল?
সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন যুগের সাথে সাথে দর্শকের মানসিক স্থিতি বদলাতে থাকে। রাজাকে প্রচ্ছন্ন রেখে নাটকের আবেদন গত নব্বই বছর ধরে দর্শকের মনকে ক্রমাগত নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে রাজাকে প্রকাশিত করে দর্শকের দরবারে হাজির করলে নাটকটির আবেদন আরও বাড়ে না কমে।
(৬)
আমি রক্তকরবীর অনেক প্রযোজনাই দেখেছি। ছোটবড় সব দলেরই। বর্তমানে কলকাতায় একটি বড় প্রযোজনা চলছে যেখানে “নন্দিনী”র ভূমিকায় শক্তিশালী অভিনেত্রী চৈতি ঘোষাল অভিনয় করছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন রসিদ খান। আর আছে আমজাদ আলী সাহেব আর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আমান আলীর যন্ত্রসঙ্গীতের সুর। অত্যন্ত ভারি প্রযোজনা এবং এই প্রযোজনাতেও দেখলাম রাজা প্রকাশিত।
ভাবলে আশ্চর্য হই এই ভেবে যে আজ থেকে প্রায় দশ-বার বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের এক মফস্বলী নাট্যদল রক্তকরবীর রাজাকে প্রকাশিত করে যে সাহস দেখিয়েছিল আজ তার প্রভাব কলকাতার বড় দলের ওপরও এসে পড়েছে।
ছোট-বড় মিলিয়ে আজ পর্যন্ত যে কটা রক্তকরবীর প্রযোজনা দেখেছি তার প্রত্যেকটাই আমাকে মুগ্ধ করেছে। এটা বোধহয় রক্তকরবী নাটকটির একটি সামগ্রিক আবেদন। বক্তব্য, বৈপ্লবিক চিন্তাধারা, সংলাপ, মানুষের দাসত্বহীন স্বাধীন জীবন যাপনের জন্মগত অধিকার এবং অতি অবশ্যই মঞ্চ উপযোগী নাট্যসাহিত্য…এই সমস্ত কিছুর সঠিক সংমিশ্রণেই রক্তকরবীর মঞ্চায়ন চিরকালীন বলেই আমার মনে হয়।
তৃপ্তি মিত্র সম্পর্কে চৈতি দেবীর মাসি হন। চৈতি দেবীর ছোটবেলার স্মৃতিতে বহুরূপীর রক্তকরবী নাটকের মহলা আর মঞ্চায়ন ভীষণ ভাবে উপস্থিত এবং এর ফলে নাটকের নন্দিনী চরিত্রে তিনি অত্যন্ত সাবলীল।
অনিল মুখোপাধ্যায়ের “বাংলা থিয়েটার ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার” বইটার “রক্তকরবী ও শিশিকুমার” অধ্যায়টাতে দেখছি “রক্তকরবী” অভিনয় করার ভার রবীন্দ্রনাথ শিশির ভাদুড়িকে দিয়েছিলেন। যে-সব কারণে শিশিরবাবু নাটকটি মঞ্চস্থ করতে পারেননি, তার মধ্যে প্রধান ছিল তখনকার শিশির-সম্প্রদায়ে নন্দিনী করার মতো কোনও অভিনেত্রীকে নাট্যাচার্যের পছন্দ ছিল না। “রক্তকরবী” না করার দুঃখ তাঁর আজীবন ছিল।
এখানে একটা বিতর্কিত বিষয় আছে, শিশিরবাবু নাকি “রক্তকরবী” নাটকটিকে একটি “হাফ ফিলজফি-হাফ থিওলজি-হাফ পলিটিক্স” রচনা বলে মনে করতেন এবং সেই কারনেই নাকি শম্ভু মিত্রকে এই নাটকটি করতে বারণ করেছিলেন। “বহুরূপী” নাট্যসংস্থার কোন একটি ক্রোড় পত্রে এই বিতর্কিত বিষয়টির দেখা মেলে। সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, তবে ভাগ্যিস শম্ভু মিত্র শিশির ভাদুড়ীর উপদেশ শোনেন নি!
রক্তকরবীর আর একটি প্রযোজনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।
স্বাধীনতা উত্তর-পূর্ব কালে দু-দুবার জর্জ বিশ্বাস মানে দেবব্রত বিশ্বাস রক্তকরবী অভিনয় করেছিলেন। সে সময়ে কালিকা সিনেমা হলে “রক্তকরবী” মঞ্চস্থ হয়েছিল। পরিচালনা জর্জের আর সেই সঙ্গে বিশুপাগলের চরিত্রে অভিনয় করলেন জর্জ। ১৯৪৭-এর শেষের দিকে শ্রীরঙ্গমেও অভিনয় হলো রক্তকরবী শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় এবং সেখানেও জর্জ বিশু। নেপথ্যে থেকে শম্ভু মিত্র রাজার ভুমিকাটি পড়লেন। শ্রীরঙ্গমে নন্দিণীর ভূমিকায় কণিকা মজুমদার ছিলেন। তৃপ্তি মিত্র অভিনয় করেছিলেন চন্দ্রা’র ভূমিকায় আর সর্দার-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।
এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি দায়বদ্ধতা হিসেবে রাজা কিন্তু মঞ্চে অপ্রকাশিতই থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির কপি রাইটের সমাপ্তি ঘটে ২০০১ সাল নাগাদ। আর তারপর থেকেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ওপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পান পরিচালকেরা।
এরপরেও বহুরূপী যখন “ছেঁড়াতার” করেছে, জর্জ তখন মহিমের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অভিনয় করতে করতে উদাত্ত কন্ঠে গান গাইতেন জর্জ। রবীন্দ্রনাথের গান জর্জের গলায় হয়ে উঠত গণসঙ্গীত। দেবব্রত বিশ্বাসের এই দিকটি আমার কাছে অপরিচিত ছিল। JU Alumni-কে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ সুশান্তকে। ওদের জন্যই কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে এই সব তথ্যের সন্ধান পাই।
যাইহোক আবার বাংলা নাটকের পট পরিবর্তনে ফিরে আসা যাক।
আস্তে আস্তে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পোস্ট রবীন্দ্রযুগে আমরা নাট্য জগতে দেখলাম এক রেনেসাঁ। ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (IPTA) তৈরি হবার পরে দেশের নাটকের চরিত্রেরই বদল ঘটে গেল। সে এক অদ্ভুত উন্মাদনা। এরপর আমরা দেখতে পেলাম সমগ্র পৃথিবীর উচ্চতম পর্যায়ের নাটকের অনুবাদ আমাদের দেশে সফল ভাবে মঞ্চে পরিবেশিত হতে থাকল। বাঙালি দর্শক ব্রেখট, কামু, কাফকা, আর্থার মিলার, গোর্কি, পিরানদেল্লো, পিটার টার্সন এবং অতি অবশ্যই শেক্সপিয়ারসহ বহু বড় বড় নাট্যকারের সৃষ্টির স্বাদ পেতে লাগল। এছাড়া আরও অনেক নামও আছে। স্থানাভাবে উহ্য রাখতে হচ্ছে।
(৭)
এইসব নাটককে ঠিক অনুবাদ না বলে রূপান্তরিত বলা বোধহয় ঠিক। কেননা এইসব নাটকের সব গল্প আর চরিত্রই আমাদের দেশে হাজির আছে শুধু তাকে আমরা দেখি বিলিতি আয়নার মাধ্যমে।
এই প্রসঙ্গে ব্রেখটের সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে।
“নাটক হলো স্বচ্ছ্ব আয়নার মতো যাতে নীল আকাশের সাথে সমাজের খানাখন্দও চোখে পড়ে। এখন আপনি আকাশ, ফুল দেখবেন, না খানাখন্দ দেখবেন কিম্বা দেখে চোখ সরিয়ে অন্য পথে যাবেন বা খানাখন্দের দায়িত্বপ্রাপ্ত কতৃপক্ষকে দোষ দেবেন অথবা আয়নাকেই গালাগাল দেবেন, সেটা আপনার রুচি। আয়না কিন্তু সত্যের প্রতিবিম্বই দেখাবে”।
আমাদের বাংলা নাট্য জগতেও এই চিন্তাধারার আঁচ এসে লাগলো।
এরপর IPTA ভেঙে গেলে আমরা পশ্চিমবঙ্গের নাট্যজগতে এক নতুন জোয়ার দেখতে পেলাম। গ্রুপ থিয়েটার নামে স্বাধীনতার পরর্বর্তী পর্যায়ে অপেশাদারি নাট্যদল তৈরির একটা চিন্তাধারা নাট্য প্রযোজনার জগতের ভিত নাড়িয়ে দিয়ে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল বলা যায় এক অদৃষ্টপূর্ব নাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে।
স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী চিন্তাধারার প্রভাব আমরা এই নাট্যআন্দোলনের দেখতে শুরু করলাম। সামাজিক সচেতনাতা বাড়াবার জন্য Have and Have-Nots-দের শ্রেণীভাগ মুছে দেবার মন্ত্রে দীক্ষা নেবার আহ্বানকে জোরদার করতে এই নতুন নাট্যকর্মীরা একের পর এক সাড়া জাগানো নাটক মঞ্চস্থ করতে লাগলেন। এনাদের মধ্যে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, অহীন্দ্র চৌধুরী, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, কুমার রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস ভট্টাচার্য এবং ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পর আমরা পাই অরুণ মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, ঊষা গাংগুলি, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, মনোজ মিত্র, অশোক মুখোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, কৌশিক সেন, শাঁওলি মিত্র, কেয়া চক্রবর্তী, মণীষ মিত্র, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পৌলমী সেনগুপ্ত, গৌতম হালদার, দেবশঙ্কর হালদার এবং আরও অনেকে (নাট্য জগতের সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বদের নাম একত্রে স্মরণ করতে না পারার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।) নিজ-নিজ গ্রুপ থিয়েটার দল প্রতিষ্ঠা করে অথবা এইসব গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করে বাংলা নাটকে শুধু যে তাঁদের প্রভূত অবদান রেখে গিয়েছেন তাই নয়, এখনও রেখে চলেছেন। বাংলা নাটক বর্তমানে তার বিশাল ঐতিহ্য স্মরণ করে যে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
১৯৪৩ সালে বিজন ভট্টাচার্যের লেখা “নবান্ন” অভিনীত হয় শম্ভু মিত্রের পরিচালনায়। সেই শুরু। সেই নাটক দিয়েই গ্রুপ থিয়েটারের জয়যাত্রা শুরু হয় বলা যেতে পারে।
১৯৪৭ সালে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায়, অহীন্দ্র চৌধুরীসহ আরও কয়েকজনের দল “বহুরূপী’ প্রতিষ্ঠীত হয়।
রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টিকে যেমন রক্তকরবী, চার অধ্যায়, বিসর্জন, ঘরে বাইরে, ডাকঘর – এঁরা নাট্যরূপে মঞ্চে এনেছেন। এছাড়া গালিলিও, পুতুল খেলা, রাজা অয়দিপাউস, রাজদর্শন, কিনু কাহারের থিয়েটার অত্যন্ত সুখ্যাত। এমনকি বহুরূপীর হালের “নালন্দা” প্রযোজনাটিও উচ্চ প্রশংসিত।
এরপর ১৯৪৯ সালে আমরা পাই উৎপল দত্তকে। বাংলা নাট্যমঞ্চে উৎপল দত্ত একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি একাধারে নট, নাট্যকার, পরিচালক, সংগঠক এবং এক প্রতিবাদী চরিত্র। তাঁর “লিটল থিয়েটার গ্রুপ” একের পর এক বৈপ্লবিক নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ইংরেজি পড়াতেন তিনি আর ছিল নাটক অন্ত প্রাণ। ১৯৪৭ সালে শেক্সপিয়ারিয়ানস নামক দল গঠন করে তিনি রিচার্ড – থ্রীতে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর সেই অভিনয় দেখে জিওফ্রে কেন্ডেল আর লরা কেন্ডেল (আমাদের পরিচিত শশী কাপুরের স্বর্গতা স্ত্রী জেনিফার কেন্ডলের বাবা-মা) এত মুগ্ধ হন যে ওনাদের “শেক্সপিয়ারিনা” নাটকের দলে উৎপল দত্তকে সঙ্গে নিয়ে দু-বছর ধরে সারা ভারত-পাকিস্তান জুড়ে অভিনয় করে বেড়ান। এরই মধ্যে ১৯৪৮ সালে উনি ব্রেখট সোসাইটি তৈরি করেন আর তার সভাপতি ছিলেন সত্যজিৎ রায়।
উৎপল দত্ত সম্পর্কে আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবে পাঠকদের কাছে কয়েকটি কথা শেয়ার করে নেওয়া যেতে পারে। IPTA-এর একজন Founder Member ছিলেন তিনি। আবার গণনাট্য সঙ্ঘেরও একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এককথায় বলা যায় বাংলার গ্রুপ থিয়েটার মুভমেন্টের প্রাণপুরুষ ছিলেন উৎপল দত্ত।
(৮)
উৎপল দত্তের “লিটল থিয়েটার গ্রুপ”(LTG) হচ্ছে প্রথম একটি গ্রুপ থিয়েটার দল যারা প্রথম একটি নাট্যমঞ্চ লিজ নিয়ে সেখানে নিয়মিত অভিনয় করে চলেছিলেন বেশ কয়েক বছর ধরে। উৎপল দত্তের “অঙ্গার” নাটকটি দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার হলে ১৯৫৯ সালে “লিটল থিয়েটার গ্রুপ” দলটির নিয়মিত অভিনয় যাত্রা শুরু হয়। গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাসে এটা একটা বড় কৃতিত্ব। এরপর ১৯৬৫ সালে উৎপল দত্তের “কল্লোল” নাটক মঞ্চস্থ হয় বিখ্যাত ভারতীয় নৌসেনা বিদ্রোহের ওপর।
তারপর ১৯৬৮ সালে “লিটল থিয়েটার গ্রুপ” ভেঙে তৈরি হয় “পিপলস লিটল থিয়েটার” (PLT) দল। এই সময়ে উৎপল দত্ত তাঁর “জনতার আফিম” নাটকে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্ম নিয়ে রাজনীতির খেলার মুলে কষাঘাত করেছিলেন। ভাবলে আশ্চর্য লাগে আজকের দিনেও ধর্ম নিয়ে রাজনীতির সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।
উৎপল দত্তই হচ্ছেন একমাত্র অভিনেতা যিনি প্যারালাল থিয়েটার ও আর্ট সিনেমা এবং কমার্র্শিয়াল হিন্দি-বাংলা সিনেমা জগতে একত্রে সফলতার স্বাদ পেয়েছেন। এটা ওনার একটা বিরাট কৃতিত্ব। প্যারালাল থিয়েটার আর আর্ট সিনেমা জগতের মানুষ মানেই যে কমার্র্শিয়াল জগতকে হীন দৃষ্টিতে দেখতে হবে সেটা তিনি ভুল প্রমাণ করে ছেড়েছিলেন।
তারপর ১৯৬০ সালে নান্দীকার জন্ম নেয়। নান্দীকার মানে হলো গিয়ে “শুভ প্রারম্ভ”। অজিতেশ, রুদ্রপ্রসাদ, কেয়া চক্রবর্তী, বিভাস চক্রবর্তী, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে এই দলটির Founder members. এই দলটির লোগোটি তৈরি করেন সত্যজিৎ রায়। “নান্দীকার” আর “নন্দন” এই দুই লোগোতেই সত্যজিতের নিজস্বতা লক্ষণীয়।
১৯৭০ সালে অজিতেশ এবং অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় নান্দীকার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও নান্দীকারের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। নান্দীকারের ঝুলিতে বহু বিদেশী নাটকের রূপান্তরিত সংস্করণ মঞ্চস্থ করার সুখ্যাতি আছে। তার মধ্যে “নাট্যকারের সন্ধানে ছ’টি চরিত্র” (মূল নাটক – পিরানদেল্লো), ফুটবল (মুল নাটক-পিটার টার্সন), শেষ সাক্ষাৎকার (মুল নাটক – ভ্লাদলেন দোজরতসেভ), ফেরিওয়ালার মৃত্যু ও গোত্রহীন (মূল নাটক-আর্থার মিলার) অত্যন্ত নামী-দামী প্রযোজনা।
বিভিন্ন সময়ের দর্শকদের চাহিদা পুরনের জন্য “ফুটবল” নাটকটি নান্দীকার তিন-তিনবার উপস্থাপিত করে। প্রথম ১৯৭৭ সালে মঞ্চস্থ হবার পর আশির দশকের মধ্যভাগে আর একবার এবং ২০০১ সালে তৃতীয়বারের জন্য “ফুটবল” আবার মঞ্চস্থ হয়। “পাঞ্চজন্য” নান্দীকারের বর্তমান কালের নতুন নাটক। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার মাঝে দাঁড়িয়ে গান্ধারী অভিযোগের আঙুল তুলেছেন কৃষ্ণের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের দিকে।
প্রথমদিকের নাটকগুলোর মধ্যে নান্দীকারের “তিন পয়সার পালা” দর্শকদের মনে চিরকালের জন্য ছাপ রেখে দিয়েছে। “তিন পয়সার পালা” নাটকটির মূল রচনাটি নিয়ে একটা ধারনা নাট্যমোদী দর্শকদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে জার্মান নাট্যকার ব্রেখট সাহেব নাকি এই নাটকটি রচনা করেছিলেন। আসলে এটি ১৭২৮ সালে জন গে নামক এক নাট্যকার এটি রচনা করেন এবং নাটকটি “দ্য বেগারস’ অপেরা” নামে প্রচলিত ছিল। ব্রেখটের সেক্রেটারি কোত্থেকে জানি এই নাটকটাকে পেয়ে সেটাকে জার্মানিতে অনুবাদ করে ফেলেন।
যে নাটক ছিল আভিজাত্যতার বিরুদ্ধে, ব্রেখট সেটাকে রাজনীতির অন্ধকার দিকগুলোর দিকে নিশানা বদল করে দেন। জার্মানিতে ১৯২৮ সালে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় এবং বিপুল জনপ্রিয়তা পাবার পর হিটলার সেটাকে বন্ধ করে দেন। বছরখানেক কি বছর দেড়েক আগে অঞ্জন দত্ত “তিন পেনি অপেরা’ নাম দিয়ে এই নাটকটি আবার কলকাতার দর্শকদের কাছে হাজির করেন।নান্দীকারের “তিন পয়সার পালা” আর অঞ্জনের “তিন পেনি অপেরা”র মধ্যে পার্থক্যটা হলো গিয়ে মূল নাটকটার না-দেশীয়করন। নান্দীকার মুল নাটকটির ভাবান্তর করে দেশজকরন করেছিল সেখানে অঞ্জন এক্কেবারে বিলিতি ঢঙে নাটকটিকে লন্ডনের প্রেক্ষাপটে হুবহু বাঙলাতে অনুবাদ করে দিয়েছেন। এটাই ছিল অঞ্জন দত্তের “তিন পেনি অপেরা’র বৈশিষ্ট।
বর্তমান বাংলা নাটক জগতে প্রচুর ভালো ভালো প্রযোজনা নাটকপ্রেমী বাঙালি দর্শককে যেমন আনন্দ দিয়ে চলেছে তেমনি ভাবাচ্ছেও। এরই সঙ্গে পুরোনো প্রযোজনা নতুন আঙ্গিকে দেখা হচ্ছে।
সময়ের সাথে সাথে নাটকের বিষয়, উপস্থাপনা এবং অভিনয়েরও চরিত্র বদল হয়েছে প্রচুর। এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বক্তব্য সম্পন্ন নাটকের পরিবর্তে নাট্যমঞ্চে এখন একটা অন্য ধরনের জোয়ার এসেছে বলেই আমার যেন মনে হয়। পৃথিবীব্যাপী উপভোক্তা সর্বস্ব অর্থনিতীর প্রভাব যেন নাট্য জগতেও এসে পড়েছে। দর্শকদের কাছে ভ্যালু ফর দেয়ার মানি জাতীয় বিনোদনের মূল্য এখন সর্বোচ্চ।
(৯)
তবে এখনও বেশ কিছু ছোট, বড় এবং মাঝারি দল তাদের বলিষ্ঠ সামাজিক বক্তব্য নিয়ে এখনও নাট্য প্রযোজনা করে চলেছেন স্রোতের উল্টোদিকে সাঁতার কাটার সমস্ত পরিশ্রম নিয়ে।
তাই এখন বাংলা নাটক জগৎ এখন আর শুধু কলকাতার নামী দামী গ্রুপ থিয়েটার-এর দলগুলোর দ্বারা প্রভাবিত নয়। বাঙলার নাট্যমোদী দর্শকদের কাছে কলকাতার ছোট আর মাঝারি দল যেমন আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনই মফস্বল আর গ্রাম বাঙলার থিয়েটার গ্রুপগুলোও সমান ভাবে বাঙলার নাটকপ্রেমী দর্শকদের আনন্দ দিয়ে চলেছে। কিন্তু আর্থিক অনিশ্চয়তা এইসব ছোট আর মাঝারি দলগুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে কেননা পেটের তাগিদে দলের সদস্যদের অনেকেরই আনুগত্যের অভাব ঘটে বড়দল, সিনেমা আর টিভি সিরিয়ালের হাতছানির কাছে।
এই প্রসঙ্গে সায়ক নাট্যগোষ্ঠীর কর্ণধার মেঘনাদ ভট্টাচার্য মাহাশয়ের কয়েকটি কথা স্মরণ করতে পারি।
“There is a tremendous inequality among groups. Some get hyped by media while some donot. Many actors & technicians work as freelancers working for several plays at the same time which dilute the quality of their work that impacts on the final performance. Some have become stars & have strong audience pull.
Big groups also enjoy media hype & spend on marketing & promotion. As a consequence, small & very good theatre groups are destroyed just when they are beginning.”
How very true it is!!!!
একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শোনাই।
বছর কয়েক আগে একটি ছোট দলের প্রযোজনা “হেলমেট” নামক একটি নাটক দেখতে গেছিলাম কোন একটা ছোট হলে। বেশ ভাল লেগেছিল নাটকটি। দর্শক সংখ্যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে শ’আড়াই হবে হয়তো।
নাটক শেষে নাটকের কর্ণধার এই দলের পরবর্তি শো অ্যাকাডেমি মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে বলে উপস্থিত দর্শকদের জানান। অনুষ্ঠানের তারিখও জানালেন সকলকে। তারপর হাতজোর করে উপস্থিত সমস্ত দর্শককে অনুরোধ করলেন যে তাঁরা যেন তাঁদের সকল বন্ধুবান্ধবদের এই নাটকের পরবর্তি শো-এর কথা জানিয়ে দেন। ছোট দল বলে ওনাদের পক্ষে বিজ্ঞাপনের খরচ বহন করা দুঃসাধ্য। অনেক তদ্বির-তদারক করে এবার অ্যাকাডেমি মঞ্চটি জোগাড় করতে পেরেছেন। তাই অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে এই অন্যায় অনুরোধটি সবার কাছে করছেন।
চোখে জল এনে দেবার মতো একটি ঘটনা। নাটকের জন্য কতটা ভালবাসা থাকলে এই ভাবে একটি নাট্যদলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ভাবলেই আশ্চর্য হতে হয়।
১৯৭৩ সালে বাংলা নাট্যজগতে “সায়ক” নাট্যদলের আত্মপ্রকাশ। অভিধানে দেখছি সায়ক কথাটির অর্থ “বাণ”, “খড়্গ”, “ব্জ্র”। “সায়ক” নাট্টগোষ্ঠীর কর্ণধার মেঘনাদ ভট্টাচার্য আমাদের বহু ভালো নাটক উপহার দিয়েছেন। সামাজিক বহু অনিয়মের বিরুদ্ধে সায়কের খড়্গ ঝলসে উঠেছে বারে বারে তাদের প্রযোজিত নাটকের মাধ্যমে।
এই হায়দ্রাবাদেই বেশ কয়েকবার অভিনয় করে গেছেন তিনি। আমি যে বছর হায়দ্রাবাদে আসি সেই ২০০১ সালেই সায়ক তার সিগনেচার নাটক “দায়বদ্ধ” আর “কর্ণাবতী” নাটক মঞ্চস্থ করে গেছে। এরপর সায়ক আবার এসেছে হায়দ্রাবাদে তাদের “পিঙ্কি বুলি” নাটক মঞ্চস্থ করতে। ২০০৪ সালে বাংলা নাট্য জগতের খ্যাতনাম অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত সায়ক-এর “সাঁজবেলা” নাটকে শ্রীময়ী’র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। মেঘনাদ-স্বাতীলেখা’র মনকাড়া দ্বৈত অভিনয় বহু নাট্যমোদীর স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল।
মেঘনাদের একটা লেখাতে একটা দামি বিষয় নজরে এলো।
পপকর্ণ মুভি কালচারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলা নাটক পরিবেশনায় অনেক বিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। নাটক প্রযোজনার খরচ এবং তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা এবং হল ভাড়া খরচ ধরে বর্তমানে যে অঙ্কটি দাঁড়ায় সেটা উদ্ধার করতে গেলে যে হারে প্রবেশ মূল্য ধার্য করতে হয় সেটা বেশীরভাগ সময়েই সাধারন নাট্যমোদী দর্শকের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। এর ফলে বাংলা নাটকের যেটা প্রধান ভিত সেই সাধারন ইন্টেলেকচুয়াল আমজনতা, তাদের বাংলা নাটক দেখার সাধ থাকলেও সেই সাধ অনেক সময়েই তাদের সাধ্যের বাইরে চলে যায়।
এর ফলে বাংলা নাটক বিতর্কিত মননশীল বিষয় থেকে দূরে সরে গিয়ে পপকর্ণ মুভি গোয়ার’সদের টেনে আনার জন্য তাদের প্রিয় বিষয় বেশিরভাগ নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিচ্ছে।
এটা কিন্তু বাংলা নাটক জগতের পক্ষে একটা অশনি সংকেত।
(১০)
এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাটা লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।
হায়দ্রাবাদে একবার গৌতম হালদারের “মেঘনাদবধ কাব্য” এসেছিল। একটা নাটক দলকে কলকাতা থেকে নিয়ে এসে তাদের থাকা-খাওয়ার সমস্ত খরচ-খরচা বহন করে, হল এবং আনুষঙ্গিক লাইট, মাইক, ষ্টেজ ক্রাফট ইত্যাদি সব খরচ ধরে এবং তারপর আয়োজিত ক্লাবের তরফ থেকে ভর্তুকি বহন করেও নাটকের প্রবেশ মূল্য বেশ যথেষ্ট বলেই সাধারন নাট্যমোদীদের মনে হয়ে থাকে।
একদা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে “মেঘনাদবধ কাব্য”-র পোষ্টার গাড়িতে লাগিয়ে ঘোরার সময় আমি মাধাপুরে একজন সাধারন “নাটক ভালবাসি” দৈনিক শ্রমিক মানুষের সংস্পর্শে আসি যাঁর বাংলা নাটক জ্ঞান দেখে আমি স্তম্ভিত হই।
২০১০ সালে গৌতম হালদার নান্দীকার ছেড়ে “৯-এ নাটুয়া” নামে নিজস্ব নাট্যদল তৈরি করেছেন। সেই দলের পক্ষ থেকে গৌতম হায়দ্রাবাদ এসেছিলেন “মেঘনাদবধ কাব্য” মঞ্চস্থ করতে।
মাধাপুরের একটি সাইটের দৈনিক শ্রমিক মেদিনীপুর নিবাসী প্রকাশ গড়াই মহাশয় আমার গাড়িতে বাংলা নাটকের পোষ্টার দেখে নিজে থেকে এগিয়ে এসে আমার সাথে আলাপ করেছিলেন নাটকটির ব্যাপারে। উনি নাটকটি ১৯৯৫ সালে কলকাতায় দেখেছিলেন যখন গৌতম নান্দীকারে অভিনয় করতেন।
ওনার সাথে নাটক নিয়ে কথা বলার সময় বুঝতে পারলাম কি অসাধারন নাটকপ্রেমী এই প্রকাশ গড়াই।
দুঃখের বিষয় ব্যক্তিগত কারণে ওনার পক্ষে আর হায়দ্রাবাদে “মেঘনাদ বধ কাব্য” আর দেখা হয়ে ওঠেনি। প্রকাশ গড়াইয়ের অনুপস্থিতির জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলাম।
মেঘনাদবাবু বাংলা নাটকের এই মননশীল নাট্যমোদী দর্শকদের কথাই বলতে চেয়েছেন। বর্তমানে বাংলা নাটকের দর্শণী অত্যধিক বৃদ্ধি হবার ফলে নিম্ন মধ্যবিত্ত নাট্যমোদী দর্শক যদি নাটক দেখা থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন তবে আখেরে কিন্তু বাংলা নাটক জগতেরই ক্ষতি। শুধুমাত্র বিনোদনের সন্ধানে বাংলা নাটকের প্রেক্ষাগৃহ উচ্চবিত্ত বাঙালি দর্শকে ভরে উঠতে থাকবে সেটা যেমন কোনো ভাবেই বাঙালি বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের কাছে কাম্য নয় তেমনি সেটা কোনো নাট্যদলই মেনে নিতে পারবে না।
এই অর্থনৈতিক চাপের প্রভাবে যে সকল বাংলা নাটক মানুষকে ভাবায়, কাঁদায়, সমাজের সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার ইন্ধন যোগায়, আস্তে আস্তে সেই সকল নাটকের উত্তাপ কমতে শুরু করবে। আর যাঁরা গাঁটের কড়ি খরচ করে উচ্চ মূল্যের দর্শণী দিয়ে শুধুমাত্র আমোদিত হতে চান, তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী আর তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য বাংলা নাটক যদি শুধুমাত্র বিনোদনের অঙ্গ হয়ে উঠতে চায় তবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা নাটক তার নিজস্ব গতিময়তা হারিয়ে ফেলবে। এই অশনি সঙ্কেতের কথাই মেঘনাদবাবু আমাদের আকারে ইঙ্গিতে আমাদের শুনিয়েছেন।
এই স্বল্প পরিসরে সমস্ত নাট্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। তাই বাংলা নাটক নিয়ে অনেক আলোচনার বিষয় থাকলেও এই রচনাটির কলেবর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকাই ভাল।
তবু আরও কয়েকটি কথা, ঘটনা না লিখলেই নয়। পাঠককূলের ধৈর্যচ্যুতি’র জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।
বাদল সরকারকে নিয়ে একটা ঘটনা পাঠকদের সাথে শেয়ার করা যাক।
গল্পটা বলেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল মশাই। বাদল সরকার আর নারায়ন সান্যাল এই দু-জন বিখ্যাত মানুষই আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।
কলেজে ছাত্রাবস্থায় নারায়ণ সান্যাল সাহিত্য চর্চার সাথে সাথে নাট্যচর্চাও করতেন। একবার কলেজে কোনো এক উৎসবে নিজেই নাটক লিখে উৎসাহী বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মহলা দেওয়া শুরু করে দেন। নাটকের দিন এগিয়ে আসছে। মহলা জোরদার চলছে। এমন সময়ে সাধারন দেখতে এক জুনিয়র ছাত্র এসে নারায়ণ সান্যাল মশাইকে ধরে বসল যে সে তাঁর নাটকে অভিনয় করবে।
যাইহোক ছেলেটির উৎসাহ দেখে শেষমেশ নারায়ণ সান্যাল রাজী হয়ে ওকে একদিন মহলায় আসতে বলেন। ছেলেটি উপস্থিত হলে তিনি তাকে নাটকের এক চরিত্রের একটি ছোট্ট পার্ট অভিনয় করে দেখাতে বলেন। ছেলেটির অভিনয় ক্ষমতা দেখে নারায়ণ সান্যাল যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে বলে বসেন যে তার দ্বারা আর যাইহোক অভিনয় হবে না।
(১১)
এরপর বেশ কিছু বছর কেটে গেছে।
নারায়ণ সান্যাল জীবনে নামী সাহিত্যক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এরকম এক সময়ে কলকাতার এক মঞ্চে নাটক দেখে খুশী হয়ে নাটক শেষে অভিনেতার প্রশংসা করতে গিয়ে জানতে পারলেন যে অভিনেতার নাম বাদল সরকার আর এই সেই অভিনেতা যাঁর অভিনয় ক্ষমতা সম্পর্কে একদা তিনি সন্দিহান ছিলেন!
বাদল সরকার তখন বাংলা নাট্য জগতে এক উজ্জ্বল জোতিষ্ক। তাঁর রচিত নাটক “বল্লভপুরের রূপকথা”, “সারারাত্রি”, “পাগলা ঘোড়া”, “এবং ইন্দ্রজিৎ” ইত্যাদি সব কালজয়ী নাটক তখন বাংলা নাট্যমঞ্চ কাঁপাচ্ছে।
নারায়ন সান্যাল মশাইয়ের তখন “ধরনী দ্বিধা হও” অবস্থা।
বর্তমান বাংলা নাট্যজগতের আর কয়েকজনের কথা না আলোচনা করলে এই রচনাটা সম্পূর্ণ হবে না বলেই আমার মনে হয়।
এঁরা দু-জনেই স্বনামে বিখ্যাত – দেবশঙ্কর হালদার আর গৌতম হালদার। দুজনেরই মঞ্চজীবন শুরু নান্দীকার থেকে।
এই মুহুর্তে বাংলা নাট্যমঞ্চে সবচেয়ে ব্যস্ত নাম হলো দেবশঙ্কর। এক সময়ে দেবশঙ্কর অভিনীত দশটিরও বেশী নাটক এবং সিনেমা একত্রে কলকাতায় নাট্যমঞ্চে ও প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের দরবারে হাজির ছিল।
আমার নিজের চোখে দেখা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সৌমিত্র কন্যা পৌলমী’র সাথে “ফেরা” নাটকে দুপুরের শো’য়ে অ্যাকাডেমিতে অভিনয় করে দেবশঙ্কর ছুটলেন উত্তর কলকাতার গিরীশ মঞ্চে সন্ধ্যার শো’য়ে ব্রাত্য বসুর “বোমা” নাটকে ঋষি অরবিন্দের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য।
যাবার আগে দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন নাটকের পরবর্তী পর্যায়ের দর্শকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত না থাকতে পারার জন্য।
হায়দ্রাবাদের নাট্যপ্রেমী দর্শক দেবশঙ্কর অভিনীত যে কটি নাটকের স্বাদ পেয়েছেন তার মধ্যে “নাচনী’, “রূদ্ধ সঙ্গীত”, “শেষ সাক্ষাৎকার” অন্যতম।
এরপর আসি গৌতম হালদারের কথায়।
“মেঘনাদবধ কাব্য” নাটকটি গৌতমের সিগনেচার আইটেম। এই নাটকটি একসময়ে বাংলা নাট্য জগতে ঝড় তুলে দিয়েছিল। কি অসাধারন একক অভিনয়! গৌতম বাঙালি দর্শকদের কাছে অভিনয় ক্ষমতার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে দেন। কি পরিমাণ প্যাশন থাকলে যে এই ধরনের উচ্চ মার্গের অভিনয় করা যায় সেটা গৌতম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।
আমরা হায়দ্রাবাদে নান্দীকারের “শেষ সাক্ষাৎকার” নাটকে গৌতম আর দেবশঙ্করের একত্রিত অভিনয় দেখেছি। নান্দীকারের “সোজনবাদিয়ার ঘাট” নাটকেও অসাধারন অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন গৌতম।
পরবর্তী পর্যায়ে “নান্দীকার” ছেড়ে নিজের নাটকের দল “৯-এ নাটুয়া” তৈরি করেন গৌতম। এই দলের “বুদ্ধু ভুতুম” নাটকটি অসাধারন। শিশু ও কিশোরদের জন্য নাটক বড় দলের খুব কমই আছে। তারা সদাই একটা ব্যবসায়িক অ-সাফল্যতার অনিশ্চতায় ভোগে। গৌতম এই মিথটির গোড়ায় কুড়ুল মেরেছেন। পরবর্তীকালে তিনি আবার “ঠাকুরমার ঝুলি” নাটকটিও মঞ্চস্থ করেন।
গৌতমের সবচেয়ে বিতর্কিত নাটকটি হলো “হাওয়াই”।
মঞ্চনির্মান, উপস্থাপনায় নাটকটিকে “জারা হটকে” নাটকের পর্যায়ে ফেলা যায়। মুল নাটকটি বিদেশী – স্লোভানীয়ার। Evald Flisar এর The Eleventh Planet এর রূপান্তর এই নাটক। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে এই নাটক। সঠিক মনে করতে পারছি না তবে নাটকের এক কুশীলবের একটি ডায়ালগ দর্শককে চিরকাল ভাবাবে বলেই আমার মনে হয়। একটি রাষ্ট্র যখন তার রণকৌশলে জয়ী হয়ে অপর রাষ্ট্রের সম্পদ অধিকার করে তখন তাকে যখন হরণ করা বলা হয় না, বলা হয় “অধিকৃত”। কিন্তু একজন সাধারন তস্কর যখন তার চৌর্য শিল্পের দ্বারা কোনো সম্পদ অধিকার করে তবে তা অধিকৃত হিসেবে বিবেচিত হবে না কেন!
এইসব কারনেই এই নাটকটিকে “জারা হটকে” নাটকের গোত্রে ফেলা যায়।
১২/-
(১২)
এবার দেবশঙ্করের নিজের জবানিতে একটা গল্প শোনা যাক।
”তখন আমি২১, নান্দীকার-এ গেছি অডিশন দিতে। বিজ্ঞাপন দেখে পাঁচশ ছেলেমেয়ে লাইন দিয়েছে। খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আমি তো অভিনয়ের কিছুই জানি না। চান্স পাব না। শেষমেশ ইন্টারভিউ দিলাম। রুদ্রপ্রসাদ আর স্বাতীলেখা অনেক প্রশ্ন করলেন,আমি কিছুই জানি না,শুধু বললাম খেলাধুলা জানি আর লিটল ম্যাগাজিন করেছি। গান গাইতে বললেন। খুব বাজে গাইলাম। কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি,আঁধার সবই মিছে। খুব রাগ হচ্ছিল ওনাদের ওপর। রেজাল্ট বেরলো। কেন দেখতে গেলাম জানি না। আশ্চর্য, আমার নাম দেখলাম লিষ্টের তলার দিকে আছে।
বেরিয়ে আসছি একজনের সঙ্গে আলাপ হল। আমারই বয়সি। শুকনো মুখ।
বললো,”আপনার হয়েছে না?
“হ্যাঁ…আপনার?“
“না হয় নি।“
“কি নাম আপনার?”
“গৌতম হালদার।“
“ভালো করে দেখেছেন?”
“না হয় নি……আমি জানি।“
“চলুন না। আর একবার দেখি…আমি দেখেছি দুজন হালদার আছে।“
‘আরে না না…জানি আমার হয় নি।“
জোর করে টেনে নিয়ে গেলাম। দেখি লিষ্টের এক নম্বর নামটা গৌতম হালদার।“”
Awesome বলা যায় কি?! নিঃসন্দেহে “হ্যাঁ” বলা যায়……তাই নয় কি?
বর্তমান নাট্য জগতের আর একজন ব্যক্তিত্বের নাম না নিলে বোধহয় বিরাট অন্যায় হয়ে যাবে। তবে উনি নাট্যমঞ্চের এবং রুপোলী পর্দার দু-দুটো তলোয়ার দুহাতে অত্যন্ত সাবলীল ভাবে এখনও ঘুরিয়ে চলেছেন – তিনি হলেন আমাদের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।
ওনার কবিতা, আবৃত্তি, ‘এক্ষণ’ পত্রিকার সম্পাদকীয়তা ইত্যাদি সমস্ত কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি ছেড়ে দিয়েও ওনার শুধু অভিনয় কুশলতাই বাঙালিকে চিরকাল বিস্মিত করে আসবে।
মঞ্চ এবং রুপোলী পর্দা – এই দুই অভিনয় জগতে সৌমিত্রবাবু নিজেকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন এবং প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন আর এক উচ্চতায় স্থাপন করে চলেছেন যে ভবিষ্যতে আর কোনও অভিনেতার পক্ষে বোধহয় এই দুই জগতের এই দুই উচ্চতায় একত্রে পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না।
এই বয়সেও সুপুরুষ সৌমিত্রবাবু যদি “রাজা লিয়র” মঞ্চস্থ করেন, তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে বাংলার নাটক পাগল দর্শক আজও রাত জেগে টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়াতে প্রস্তুত।
সৌমিত্রবাবুর প্রথম নাটক আমি দেখি “নামজীবন”…মানিকতলার কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে। হলের Acoustic অত্যন্ত খারাপ ছিল। পেছনের দর্শক সংলাপ শুনতে পাচ্ছেন না, বিরক্ত হচ্ছে্ন। শেষমেশ মাইক বন্ধ করেই নাটক শেষ করলেন তিনি। দর্শক আর গোলমাল করেনি।
এরপর ওনার অভিনীত “নীলকণ্ঠ”, “হোমাপাখি”, তৃতীয় অঙ্ক অতএব” এবং হালের “ফেরা” নাটক দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এই বয়সেও উনি নিজেকে সিরিয়াস নাটকের সাথে এত গভীর ভাবে কি করে জড়িত রেখেছেন এটা ভাবলেই আশ্চর্য লাগে।
সত্যি বাংলা এবং বাঙালির গর্ব হচ্ছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।
(১৩)
বাংলা নাটক জগৎ বলা যেতে পারে সতত জঙ্গম। প্রতিনিয়ত এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। স্বদেশী, বিদেশী, মাইথলজি, রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সবরকম বিষয়বস্তু নিয়েই কোন না কোনও দল তাদের নিত্য নতুন ভাবনা চিন্তা নিয়ে বাঙালি দর্শকদের কাছে হাজির করে চলেছেন তাঁদের নতুন নতুন নাটক।
এই রকমই একটি নাটকের নাম “উরুভঙ্গম”। মণীশ মিত্রের সারারাত্রি ব্যাপি ছ’ঘন্টার নাটক নিয়ে বাঙলার নাট্য জগতে এক নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল। মঞ্চে বিদ্যমান সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে বিশাল একটি নাট্য দলের যথেষ্ট পরিশ্রমী উপস্থাপনা। মোট চারটে ব্রেক আছে এই নাটকে এবং এই সময়ে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে দর্শকদের মধ্যে কথকথার মাধ্যমে সঙ্গীত শিল্পীসহ নাটকটি পরিবেশিত হয়। এটি একটি ব্যতিক্রমী পরিবেশনা বলা যেতে পারে।
এতক্ষণ ধরে বাংলা নাটকের পরিচিত বড় বড় নামি-দামী দলের আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম। এবার একটু কলকাতা সংলগ্ন এবং কলকাতার বাইরের কিছু ছোট ছোট দলের নাটকের কথা শোনা যাক। নামে এবং ওজনে এইসব দল হয়ত বড় ব্ড় দলের সাথে এক পংক্তিতে বসতে পারে না বটে কিন্তু চিন্তায় ভাবনায় পরিবেশনায় এই দলগুলি কিন্তু বড় বড় দলগুলির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে।
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যে দলটির কথা আমার মনে আসছে সেটা হল “গোবরডাঙার নকশা”। এই দলটির “স্বপ্ন স্বদেশ” নাটকটির বক্তব্যে দেশের স্বাধীনতা বিষয়ক মূল উপলব্ধির গোড়ায় আঘাত করে।
সেইরকমই কল্যাণীর একটি দলের প্রযোজনা “খোয়াবনামা”। মঞ্চ পরিকল্পনায় যে কোন বড় দলকে এরা লজ্জায় ফেলে দিতে পারে।
নিজেদের সীমিত ক্ষমতার উর্ধে উঠে এইসব দল শুধুমাত্র নাটকের প্রতি ভালবাসার দায়বদ্ধতার জন্য একের পর এক মনকাড়া নাটক নিয়ে দর্শকদের ভাবনা চিন্তাকে নাড়িয়ে দিতে হাজির হয়।
এইরকম বেশ কিছু দল আছে যারা তাদের নাটকের মাধ্যমে নাটকপ্রিয় মননশীল দর্শককে ভাবায়, কাঁদায়, চিন্তা করতে শেখায় এবং অবশ্যই “থোড়-বড়ি-খাড়া / খাড়া-বড়ি-থোড়” ক্লিশে জীবন যাত্রার বাইরেও যে একটা সুস্থ্য সুন্দর জীবন আছে সেটা দেখতে বুঝতে সাহায্য করে।
এইরকমই কয়েকটি মফস্বলী দল হল “কৃষ্ণনগর সিঞ্চন”, “সমতট সংস্কৃতি – উত্তরপাড়া”, “রঙ্গপীঠ-শান্তিপুর”, “সপ্তর্ষি-বহরমপুর”।
এদের মধ্যে “সপ্তর্ষি-বহরমপুর” বছর কয়েক আগে হায়দ্রাবাদে সিরাজদৌল্লার জীবন নিয়ে তাদের নিজেদের রচনা এবং প্রযোজনা “মতিঝিলের কান্না” পরিবেশন করে গেছেন। বহরমপুরের সৈদাবাদে এই নাট্যদলটির আঁতুড় ঘরে আমি গিয়ে মুদ্ধ হয়েছি। দেখেছি কি ভীষণ পরিমাণে উৎসর্গীত প্রাণ না হলে এই ধরনের নাট্যদলকে বাঁচিয়ে রাখা কতখানি দুরূহ। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় অসম্ভব।
এইসব নাট্যদলের নিরলস নাট্যচর্চা আছে বলেই বাংলা নাটক জগত আজও এত সমৃদ্ধ।
সবশেষে আমাদের হায়দ্রাবাদের একটা নাট্যদলের কথা বলে এই রচনাটিতে দাঁড়ি টানতে চাই।
সুদূর প্রবাসে হায়দ্রাবাদের বাঙালিকে সিরিয়াস নাটক-রসের স্বাদ আস্বাদন করানোর প্রচেষ্টায় “শূদ্রক-হায়দ্রাবাদ” নাট্যদল নিয়মিত কিছু বলিষ্ঠ নাটক পরিবেশন করে চলেছে। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এই দলের কর্ণধার স্বপন আর পুলকের নিরলস প্রচেষ্টা অতি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।
এই দলটির বাংলা নাটক “এক স্বৈরাচারী রাজার কথা”, “আজীর” এবং “সারারাত্রি” সমালোচকদের বিস্মিত করেছে। এছাড়া আরও অনেক অন্যভাষী নাটক ভারতবর্ষের দর্শকদের মনের কোনায় চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে।
এই দলটির সাথে একবার শান্তিপুরে তিনদিন ব্যাপী নাট্যউৎসবে দুদিন হাজির থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এই দেখে যে শান্তিপুরের মত একটি ছোট শহরে এত বিরাট একটা নাট্যউৎসব আয়োজন করা কি করে সম্ভব!
সারা ভারতবর্ষ থেকে কত নামীদামী নাট্যসংস্থা শান্তিপুরের এই বাৎসরিক নাট্যউৎসবে যোগ দিতে উদগ্রীব হয়ে থাকে।
সুদূর পাঞ্জাব, আহমেদাবাদ, ত্রিপুরা, NSD Reparatory-দিল্লী, কর্ণাটক, বাংলাদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, পন্ডিচেরি থেকে শান্তিপুরের ২০১৬ সালের এই নাট্য উৎসবে হাজির হয়েছিল।
এছাড়াও ঊষা গাঙ্গুলি (অন্তর্যাত্রা), সুমন মুখোপাধ্যায় (ম্যান অফ দ্য হার্ট) এবং অশোক মুখোপাধ্যায় (কুশীলব) এর মত কলকাতার নামীদামী নাট্যব্যক্তিত্ব শান্তিপুরের এই নাট্যউৎসবে নিজেদের নাটক নিয়ে হাজির ছিলেন।
(১৪)
সবচেয়ে যেটা ভালো লাগল সেটা হচ্ছে ছোট্ট শহর শান্তিপুরের এই নাট্যউৎসব ঘিরে সে কি উন্মাদনা। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-বউ সবাই যেন কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শান্তিপুরের এই নাট্যউৎসবকে সফল করার জন্য। এই নাট্যউৎসবের প্রাণপুরুষ বিশ্বজিৎবাবু ও তাঁর নাট্যদল রঙ্গপীঠ-এর আন্তরিক প্রচেষ্ঠা অতি অবশ্যই প্রশংসনীয়।
সবশেষে মনে হয় রঙ্গপীঠের মত বেশকিছু নাট্য সংস্থা আজ আমাদের পশ্চিমবাংলায় আছে বলেই বাংলা নাটক আজও তার ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে পেরেছে।
দু হাত জোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সারা পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বজিৎবাবুরা এবং তাঁদের নাট্যদলগুলি আগামী দিনে আরও বড় হয়ে উঠুক আর বাংলা নাটকের ইতিহাস ওনাদের আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক।
পরিশিষ্টঃ এই রচনায় বাংলা নাট্য জগতের একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরার অসফল প্রচেষ্টা আছে মাত্র। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে মুলত গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন এবং সমসাময়িক বাংলা নাটকের কথা বলতে গিয়ে এই রচনাটিতে শুধুমাত্র প্যারালাল থিয়েটারের কথাই এসে গেছে। কিন্তু বাংলা নাট্য জগতে এটাই শেষ কথা নয়। এই প্যারালাল থিয়েটারের সাথে সাথে বাণিজ্যিক বহু থিয়েটারও বাংলা নাট্য জগতের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কলকাতার বাণিজ্যিক মঞ্চ ভাড়া করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে বাংলা বাণিজ্যিক নাটক দর্শকদের মনোরঞ্জন করে এসেছে। সারকারিনা, তপন থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটারে বারবধু, নহবত, বিবর, লাগলে বলবেন, কড়ি দিয়ে কিনলাম, সাহেব বিবি গোলাম ইত্যাদি বহু নাটকের বলিষ্ঠ প্রযোজনা আমরা দেখেছি। সুপ্রিয়া / সাবিত্রী / তরুণ কুমার / ভানু / জহর / বিকাশ রায় / উত্তম কুমার / অনুপ কুমার / রবি ঘোষ / চিন্ময় রায় এবং বাঙালী চলচিত্র জগতের আরও অনেক নামীদামী অভিনেতা-অভিনেত্রী বাংলা বাণিজ্যিক নাটক জগতকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।
ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে সময় সুযোগ হলে মিস শেফালি, মিস জে সহ সকল নৃত্যশিল্পীদের অগ্নিময় উপস্থিতি এবং বাণিজ্যিক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় নিয়ে আরও কিছু লেখার।
বাকি থেকে গেল বাংলা থিয়েটারের গান। এটা বলা যেতে পারে বাংলা সাঙিস্কৃতিক জগতে একটা আনমোল রতন। এটা আমার সামর্থের বাইরে। বাংলা নাটকের এই দিকটা নিয়ে যদি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি কলম ধরেন তো হায়দ্রাবাদের সকল বাঙালিই উপকৃত হবেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিজের গলায় তাঁর “নীলকন্ঠ” নাটকে গান গেয়েছিলেন বছর ত্রিশ(+) আগে। সেই নাটক দেখার সৌভাগ্য এই অধমের হয়েছিল।